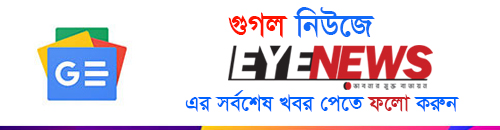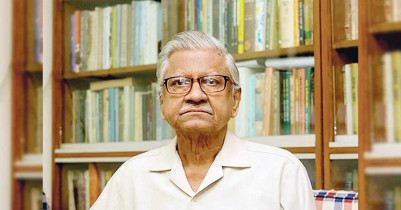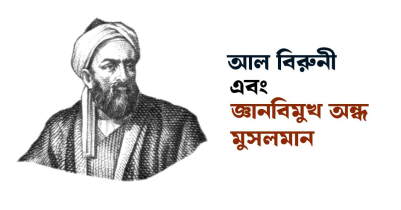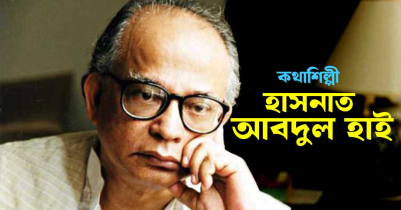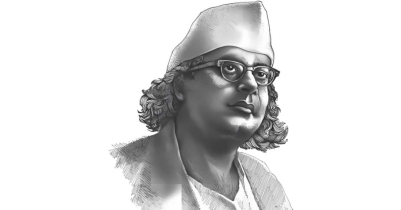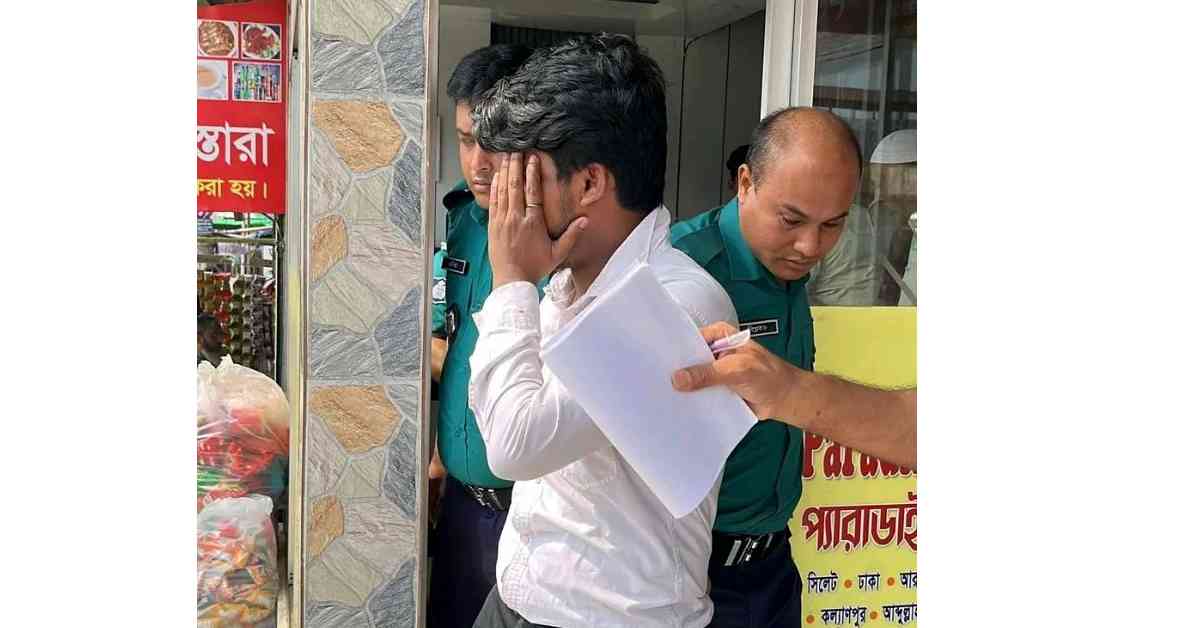শ্যামলাল গোঁসাই
আপডেট: ১৮:৪০, ১৮ জানুয়ারি ২০২১
শিবপাশার লোককবি ইব্রাহীম ও আমাদের লোকসাহিত্য

গ্রামীন যাপিত জীবনবোধ, প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ, সাম্প্রতিক ঘটনার সাথে আঞ্চলিক উপাদান নিয় গড়ে ওঠে লোক সংস্কৃতির অবকাঠামো কিংবা লোকসাহিত্য৷ সাহিত্যের এই ভাগটিতে এসে লোককবি বা বাউলদের সহজ-সরল আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার,সুমিষ্ট সুরের প্রয়োগে গ্রামীন জীবনের চিরায়ত ঘটনা বা গল্পগুলো আমাদের কাছে হয়ে ওঠে সহজপাঠ্য।
মূল খুঁজলে দেখা যাবে এগুলোই ছিলো আমাদের বাঙলা সাহিত্যের আদি কবিতা। কারণ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে যা কিছুই রচনা করা হয়েছে তা গাওয়ার উদ্দেশ্যে, পড়ার উদ্দেশ্যে। আমরা কবিতাকে গদ্য আকারে পড়তে শুরু করলাম যখন বাঙলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো আশ্চর্য প্রতিভারা কলম ধরলেন। এর আগ পর্যন্ত আমরা কবিতা গেয়েছি সুরের সাথে।
আর তাই লোকসাহিত্যের বেশিরভাগ অংশ খাতায় লিখা থাকুক বা নাই থাকুক গ্রামের মানুষের মুখে মুখে তা থাকবেই। একারণে এদেশের সুফি, সাধক, বাউল, লোককবিরা যেসব পদ বা গান রচনা করেছেন এর যতোটা না খাতায় লিখিত অবস্থায় পাওয়া গেছে তারচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে।
এদেশের গ্রামের কৃষকরা ক্ষেতে কাজ করতে করতে গলায় যে সুর তোলে নিয়েছেন, যে গান গেয়েছেন তা লোকসংস্কৃতির অংশ। কিংবা রাখাল বালক সন্ধায় গরু নিয়ে ফিরতে ফিরতে যে গান গেয়েছে সেখানেও রয়েছে লোক সাহিত্যের রস।
লোককবিদের এসব গানে কখনো ফুটে ওঠেছে গ্রামীন জীবনের গল্প। আবার কখনো ফুটে স্রষ্টাকে না পাওয়া ব্যাকুলতা। গানে গানে কখনো কখনো লোককবিরা নিজেদের সঁপে দিয়েছেন স্রষ্টার ছায়াতলে, আবার কখনো নিজের দেহের ভেতরেই খোঁজে বেড়িয়েছেন স্রষ্টাকে। সেখান থেকে লিখেছেন গান।
আদিকাল থেকে লোককবিরা তাদের এসব সহজ রচনা দিয়ে সমৃদ্ধ করে আসছেন বাংলা সাহিত্যকে। এই লোককবিদের কেউ কেউ অতিমাত্রায় খ্যাত হয়েছেন কেউ আবার থেকেছেন অখ্যাত। তবুও থেমে থাকেনি লোককবিদের যাত্রা। আব্দুল করিম, রাধারমন, হাসন রাজা, শিতালং শাহসহ অন্যান্য লোককবিদের সেই ধারাকে বাংলা সাহিত্যে তাদের পরে আরো অনেকেই বয়ে আনছেন এবং আনবেনও। কারণ আমাদের লোকসাহিত্যের ভান্ডার এতো বড় যে তা হুট করেই শেষ হয়ে যাবার নয়।
আমাদের লোক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও এমনি। একজন লোককবি তা নির্মাণ করলেও সেখানে থাকে পুরো সমাজের প্রতিচ্ছায়া কিংবা জীবনের গল্প। যেই গল্প শহরের বনসাই জীবনে থেকে পাঠ করা সম্ভবপর নয়।
তেমনি এক লোককবির নাম ইব্রাহীম। সবাই যাকে চেনে ইব্রাহিম ড্রাইভার নামে। এই মানুষটি গান গেয়ে তাঁর যাত্রী, সহকর্মীদের আনন্দ দেন। আমি যখন হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে যাই তখন ঘটনাচক্রে হাওর পাড়ের এই মানুষটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়।
তাঁর জন্ম আজমিরিগঞ্জের শিবপাশা গ্রামে। গ্রামের চৌদিকে হাওরের জলের হাতছানি। তার মধ্যে থেকেই তিনি রচনা করে চলেছেন একের পর এক গান। আড্ডা দিতে দিতে জানতে পারলাম তাঁর জীবনের করুণ এক গল্প।
বছর চারেক আগে তাঁর এক ছোট ভাই সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান। যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। এই ভাইয়ের নির্মম মৃত্যুর পরে ভাইয়ের শোকে অন্যরকম হয়ে যান ইব্রাহীম। ভাইয়ের শোকে রচনা করেন ‘ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন’ গান।
ভাইয়ের শোকে শোকাতুর হয়ে ইব্রাহীমের গান লিখা শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে ইব্রাহীম গানের অন্যান্য দিকগুলোতেও দৃষ্টি দেন। ধীরে ধীরে গড়ে তোলতে থাকেন নিজের গানের বলয়। আব্দুল করিমের মতো ইব্রাহীমও তার গানের অবকাঠামোতে জুড়ে দিয়েছেন আঞ্চলিক উপমা। আর এসব আঞ্চলিক উপমা গানকে যেমন করে তোলেছে উপভোগ্য তেমনি স্রোতার কাছে গানের মূলতত্বটিকে করেছে সহজপাঠ্য। তার গানে প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ গ্রামীন জীবনের ছাপ। রয়েছে সৃষ্টির চিরায়ত নিয়ম মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার স্বীকারোক্তি। একারণে ইব্রাহীমের গানে তিনি বলেন, 'এমন একদিন আসবে রে মন/ ভাই বন্ধু সব হইবো পর/ আমার জন্য তৈয়ার করো/ সাড়ে তিনহাত মাটির ঘর।'
ছোটভাই মারা যাওয়ার পরে ইব্রাহীমের গান লেখা শুরু হয়। কিন্তু নিজে গাইতে জানেন না বলে গানগুলো অপ্রকাশিতই থেকে যাচ্ছিলো। শিল্পী মহসিন দেওয়ান তার একটি এলবামে ভাইকে নিয়ে লিখা, 'ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন' গানটি গাইলে বেশ সাড়া পান ইব্রাহীম।
গানের এমন সহজ-সরল ভাষার ব্যবহার তার গানকে করে তোলেছে আরও প্রাঞ্জল। ইব্রাহিম এরপরে লিখেছেন আরো অনেকগুলো গান। যেগুলোতে রয়েছে তীব্র জীবনবোধ, দুঃখ, কষ্ট, প্রেম-বিরহ। তবে এগানগুলো সংগ্রহ এবং না অপ্রকাশিত থাকার কারণে হয়তো হারিয়ে যাবে আমাদের লোকসাহিত্য থেকে। সেই সাথে হারিয়ে যাবে লোককবি ইব্রাহীমও।
আগেই বলেছি ইব্রাহীম তার গানের বলয় তৈরি করেছেন আঞ্চলিক উপাদানে৷ যেমন তার একটা গানের শেষ দিকে তিনি বলছেন, 'আমার মায়ে কাঁদবে জারে জারে/ বাবা বলবে হাতটা ধরে/বিদায় দাও আমার সন্তানরে/ এই বুঝি তার শেষ নাইওর।' এখানে 'নাইওর' শব্দটি গ্রামীন একটা শব্দ।
মূলত এখনো যেইসব এলাকা ছয় মাস পানিবন্দী অবস্থায় থাকে এবং ছয় মাস শুকনা সেসব এলাকায় এই 'নাইওর' এর পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। ভাটি এলাকায় এখনো নারীরা বর্ষার সময় নতুন পানি আসলে স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে যান। 'স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি যাওয়া'র এই বিষয়টিকে 'নাইওর' বলা হয়ে থাকে। ইব্রাহীম তার গানে মৃত্যুর সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন এই নাইওর শব্দটিকে। তিনি তার মৃত্যুকেও শেষ নাইওর বলছেন। আসলেও তাই!
আমরা জানি যে লোককবিদের রচিত গান বা পদে বেশিরভাগ সময়েই প্রতীকী শব্দের ব্যবহার করেন তারা। এটিকে লোকসাহিত্যের অলংকার হিশেবে ধরা যেতে পারে। লোককবিরা তাদের গানে অনেক সময় একটি বিষয়কে প্রকাশ করতে এর মূল শব্দ রেখে প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেন। ঠিক তাই করেছেন ইব্রাহীম তার গানে। তিনি তার মৃত্যুকে প্রকাশ করছেন নাইওর শব্দটির মাধ্যমে। কারণ নারী যেমন স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি যায় তেমনি সৃষ্টির চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীকে এই জগত সংসার ছেড়ে অনাদীকালের সেই কৃষ্ণগহ্বরে যেতে হবে। পুরো ব্যাপারটিই গ্রামের সেই 'নাইওর' শব্দটির সাথে মিলে যায়। তাই ইব্রাহীম সরাসরি 'মৃত্যু' না বলে 'নাইওর' শব্দটিই বেছে নিয়েছেন। আর এভাবে ইব্রাহীম গড়ে তোলেছেন গানের অবকাঠামো। গ্রামীন অলংকারে সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন গানের। গানে জন্ম দিয়েছেন নতুন রসের। যেই রস বাংলা সাহিত্যকে হয়তো আরো সমৃদ্ধ করবে। যেমনটা করেছিলেন ইব্রাহীমের পূর্ববর্তী সুফি, বাউল,সাধক, লোককবিরা।
ইব্রাহিম পেশায় একজন অটো ড্রাইভার। টানা-পোড়নের সংসারের থেকে জীবনের একটা গভীর অভিজ্ঞতা আছে তার। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি তার গান রচনার ক্ষেত্রে। জীবনের দিকগুলোকে ফুটিয়ে তোলেছেন গানে। যা হয়তো একসময় গ্রামের আরো দশজন হাভাতে মানুষের জীবনের কথা হিশেবে বিবেচ্য হবে।
আমাদের লোক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও এমনি। একজন লোককবি তা নির্মাণ করলেও সেখানে থাকে পুরো সমাজের প্রতিচ্ছায়া কিংবা জীবনের গল্প। যেই গল্প শহরের বনসাই জীবনে থেকে পাঠ করা সম্ভবপর নয়।
- কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ: বাঙলা ভাষার প্রথম বই
- জীবনানন্দ দাশের কবিতা: বৃক্ষ-পুষ্প-গুল্ম-লতা (শেষ পর্ব)
- জীবনানন্দ দাশের কবিতার পাখিরা
- দুঃখের নাগর কবি হেলাল হাফিজ
- সমরেশ মজুমদার এবং ২টি কবিতা
- সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ৯ দিনব্যাপী অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা
- পিকলু প্রিয়’র ‘কবিতা যোনি’
- মাকে নিয়ে লিখা বিখ্যাত পঞ্চকবির কবিতা
- হ্যারিসন রোডের আলো আঁধারি
- গল্পে গল্পে মহাকাশ
মেজোমামা খুব বোকা