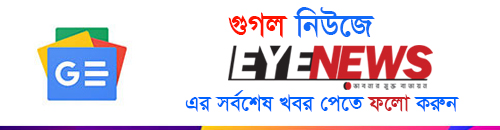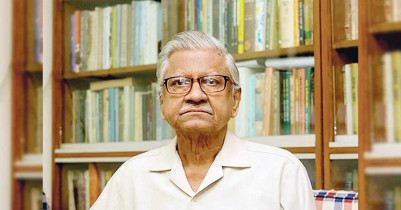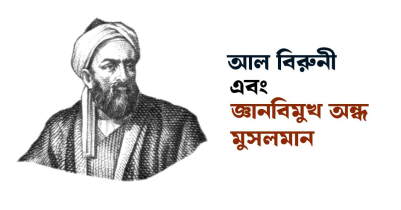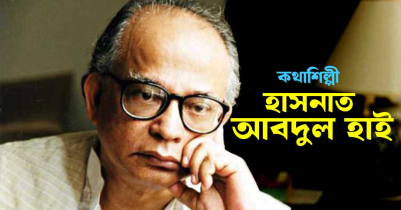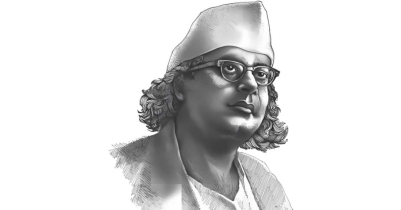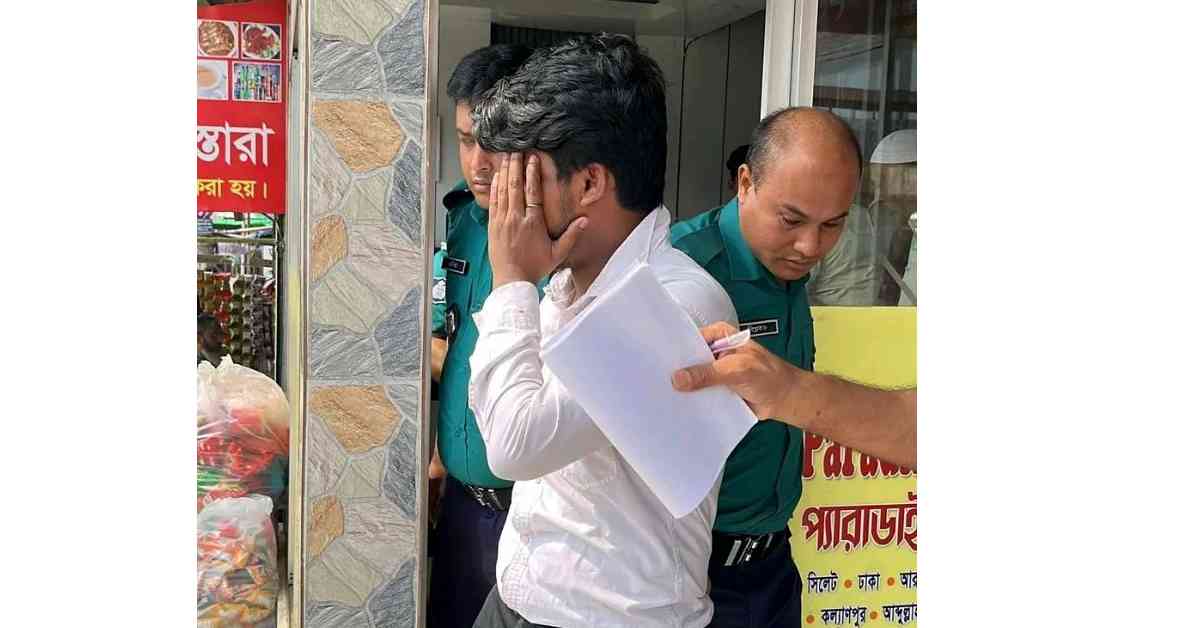মোহাম্মদ আবদুল খালিক
আপডেট: ২২:২৯, ১ অক্টোবর ২০২১
জীবনানন্দ দাশের কবিতা: বৃক্ষ-পুষ্প-গুল্ম-লতা (পর্ব ২)

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৬ বৈশাখ রোহিনীকুমার গুপ্তের কণ্যা লাবণ্য গুপ্তের (১৯০৯-১৯৭৪) সঙ্গে ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে জীবনানন্দ দাশের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাঁর এক কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ এবং একমাত্র পুত্র সমরানন্দ দাশ। কলকাতা জীবনে স্ত্রী লাবণ্য দাশ শিক্ষকতা করেছেন। অনেকের মতে তিনি অনেকটা স্বেচ্চাচারী ও উচ্চাভিলাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং এতে করে তাঁদের দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখের ছিল না।
ভূমেন্দ্র গুহ লিখেছেন,
‘জীবনানন্দের মৃত্যুর পর লাশ তখনও বাড়িতে ... এক সময়ে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ আমাকে ঝুলবারান্দার কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব বসু এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তাহলে তোমার দাদা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কি রেখে গেলেন বলো তো।’ (৫)
তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘বর্ষা আবাহন’ ব্রাম্মবাদী পত্রিকার ১৩২৬ সনের (১৯১৯খ্রি.) বৈশাখ সংখ্যায় বের হয়। শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি জীবনানন্দ দাশ এই নামে লিখতে শুরু করেন। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশ লোকান্তরিত হলে ‘দেশবন্ধু প্রয়াণে’ শিরোনামযুক্ত একটি কবিতা লিখেছিলেন-যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় ১৩৩২ সনের (১৯২৬ খ্রি.) শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে দীনেশ রঞ্জন দাশ সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় ১৩৩২ সনের (১৯২৬খ্রি.) ফাল্গুন সংখ্যায় নীলিমা শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার আসরে জীবনানন্দ দাশের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় বলে অনেকেই মনে করেন। ‘প্রকাশিত, অপ্রকাশিত লেখা যোগ করলে দেখা যাচ্ছে, তিনি লিখেছেন প্রায় আড়াই হাজার কবিতা, গোটা বিশেক উপন্যাস, শতাধিক গল্প, পঞ্চাশটির উপর প্রবন্ধ আর প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার ডায়রি, যাকে তিনি বলেছেন- ‘‘লিটারারি নোটস’’। (৬)
জীবদ্দশায় প্রকাশিত কাব্য
- ঝরাপালক (১৯২৭)
- ধূসর পান্ডুলিপি (১৯৩৬)
- বনলতা সেন (১৯৪২)
- মহাপৃথিবী (১৯৪৪)
- সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)
- বনলতা সেন (পরিবর্ধিত সংস্করণ) (১৯৫২)
- জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)
- প্রবন্ধ- কবিতার কথা (১৯৩৮)
মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত কাব্য
- রূপসী বাংলা (১৯৫৭)
- বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)
- সুদর্শন (১৯৭৩)
- আলো পৃথিবী (১৯৮১)
- মনো বিহঙ্গম হে প্রেম (১৯৯৮)
- তোমারে ভেবে ভেবে (১৯৯৮)
- অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯)
- আবছায়া (২০০৪)
মৃত্যু পরবর্তী সময়ে স্যুটকেস বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্প সমূহ। প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-
কল্যাণী, মৃণাল, বিভা, কারুবাসনা, জলপাইহাটি, মাল্যবান, বাসমতির উপাখ্যান, সুতীর্থ, বিরাজ ইত্যাদি।
১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ‘বনলতা সেন’ এর সিগনেট সংস্করণ ১৩৫৯ সনের শ্রেষ্ঠ কাব্য বিবেচনায় নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কারে ভূষিত হয়।
১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুর পর ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (১৯৫৪) সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।
১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রি. তারিখে কলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। জীবনানন্দের চিৎকার শুনে নিকটস্থ চায়ের দোকানের মালিক চুনীলাল এবং অন্যরা তাঁকে উদ্ধার করে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ সময় ডা. ভূমেন্দ্র গুহ সহ অনেক তরুণ কবি জীবনানন্দের সুচিকিৎসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রি. তারিখ রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। এটাকে অনেকেই স্রেফ দুর্ঘটনা হিসেবে দেখতে চাননি।
(২)
গ্রাম বাংলর ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পূরাণের জগৎ জীবনানন্দের কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। এতে করে তিনি রূপসী বাঙলার কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে ‘নির্জনতম’ কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্নদা শংকর রায় বলেছেন ‘শুদ্ধতম কবি’। এছাড়াও সমালোচকদের অনেকেই তাঁকে রবীন্দ্রনাপথ ও নজরুল পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি বলে অভিহিত করে থাকেন। নিসর্গ সচেতন কবি জীবনানন্দ দাশ বৃক্ষ-পুষ্প-গুল্ম-লতা ইত্যাদির ব্যাপক এবং সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর গদ্য ও কবিতায়। পৃথিবীর এক অনন্য স্থান হিসেবে নৈসর্গিক চিত্ররূপময়তায় আঁকতে চেয়েছেন অপরূপ রূপসী বাংলাকে-
এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে- সব চেয়ে সুন্দর করুণ:
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম: কাঁঠাল, অশ^ত্থ,বট, জারুল হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
... ... ...
সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
... ... এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খোঁজে তুমি পাবে নাকো- বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।
(রূপসী বাংলা. ২৮)
একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ করলে আমরা দেখব অন্যান্য কাব্য ও পুস্তকাদির প্রসঙ্গ বাদ দিলেও একমাত্র রূপসী বাংলা কবিতাগ্রন্থে যেসব বৃক্ষ-পুষ্প-গুল্ম-লতা ইত্যাদির নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে- এ তালিকা একবারে ছোট নয়। দেশের বৃক্ষ-পুষ্প-গুল্ম-লতার বৃহৎ অংশের নামই এখানে উঠে এসেছে বলেই মনে হবে। যেমন:-
চালতা, কাঠাল, হিজল, তাল, তমাল, তেঁতুল, শিমূল, জাম, জামরুল, বট, অশ^থ, পাম, পলাশ, গাব, বাবলা,ঝাউ, করমচা, নিম, বেল, সুপুরি, নারকেল, বাঁশবন, শ্যাওড়া, জারুল, সজিনা, চন্দন, লিচু, আতাবন, ডুমুর, মহুয়া, এলাচি, দারুচিনি, কামরাঙা, কলমীলতা, ফণিমনসা,শটিবন, ভাঁটফুল, ঢেঁকি শাক, সর্ষেক্ষেত, চিনি চাঁপা, লেবু, আনারস, পুঁইলতা, বেগুন, কুল, বইচি, লাল শাক, পাট শাক, হেলেঞ্চা, শেফালি, কাঁঠালিচাঁপা, ভেরেন্ডা, মাদার, শসালতা, কাঠমল্লিকা, জামীর, বাসমতিচাল, শালিধান, রূপশালিধান, করবি, অপরাজিতা, পদ্ম, গোলাপ, কদম, আকন্দ, বাসকলতা, বেতফল, নোনা ফল, নাটাফল, ধুন্দুল, চাঁপাফুল, অশোকলতা, দ্রোণফুল, মৌরী, শরেরবন, মাকাল লতা, ঘাস ইত্যাদি পরিচিত অপরিচিত অনেক বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফসল ও ফলের কথা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উঠে এসেছে।
শটি ফুল সম্পর্কে বিপ্রদাশ বড়–য়ার অভিমত- ‘শটিফুলের চমৎকার ফুলটি নিয়ে বোধ করি জীবনানন্দ দাশই শুধু কবিতা লিখেছেন’। এছাড়াও বিপ্রদাশ বড়–য়া মনে করেন,-‘জীবনানন্দ দাশ আকন্দ, ধুন্দুল, ঢেঁকি শাক,নাটা, কুশ,আর কাশকে রূপসী বাংলা কাব্যে ব্যবহার করে আমাদের অবহেলার উত্তর দিয়েছেন’ (৭)
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি-চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ
জাম- বট- কাঁঠালের-হিজলের- অশ^ত্থের করে আছে চুপ:
ফণিমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিলে;
(রূপসী বাংলা, ৪)
কিংবা,
মাঠ থেকে গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস
ভেসে আসে;-ডানা তুলে সাপমাসী উড়ে যায় আপনার মনে
আকন্দ বনের দিকে;
(ধারাবাহিকভাবে আইনিউজে এই আলোচনাটি চলবে...)
মোহাম্মদ আবদুল খালিক, সাবেক অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ।
তথ্যসূত্র ও ঋণ স্বীকার:
৫. ভূমেন্দ্র গুহ, জীবনানন্দ: আবু তাহের মজুমদার ২০০২, থেকে উদ্ধৃত ]
৬. শাহাদুজ্জামান: পূর্বোক্ত
৭. বিপ্রদাশ বড়ুয়া: গাছ পালা তরুলতা ২০১২
- কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ: বাঙলা ভাষার প্রথম বই
- জীবনানন্দ দাশের কবিতা: বৃক্ষ-পুষ্প-গুল্ম-লতা (শেষ পর্ব)
- জীবনানন্দ দাশের কবিতার পাখিরা
- দুঃখের নাগর কবি হেলাল হাফিজ
- সমরেশ মজুমদার এবং ২টি কবিতা
- সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ৯ দিনব্যাপী অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা
- পিকলু প্রিয়’র ‘কবিতা যোনি’
- মাকে নিয়ে লিখা বিখ্যাত পঞ্চকবির কবিতা
- হ্যারিসন রোডের আলো আঁধারি
- গল্পে গল্পে মহাকাশ
মেজোমামা খুব বোকা