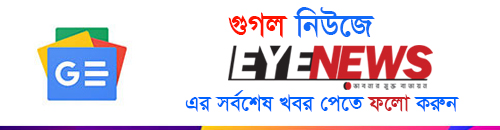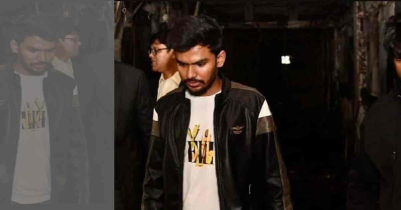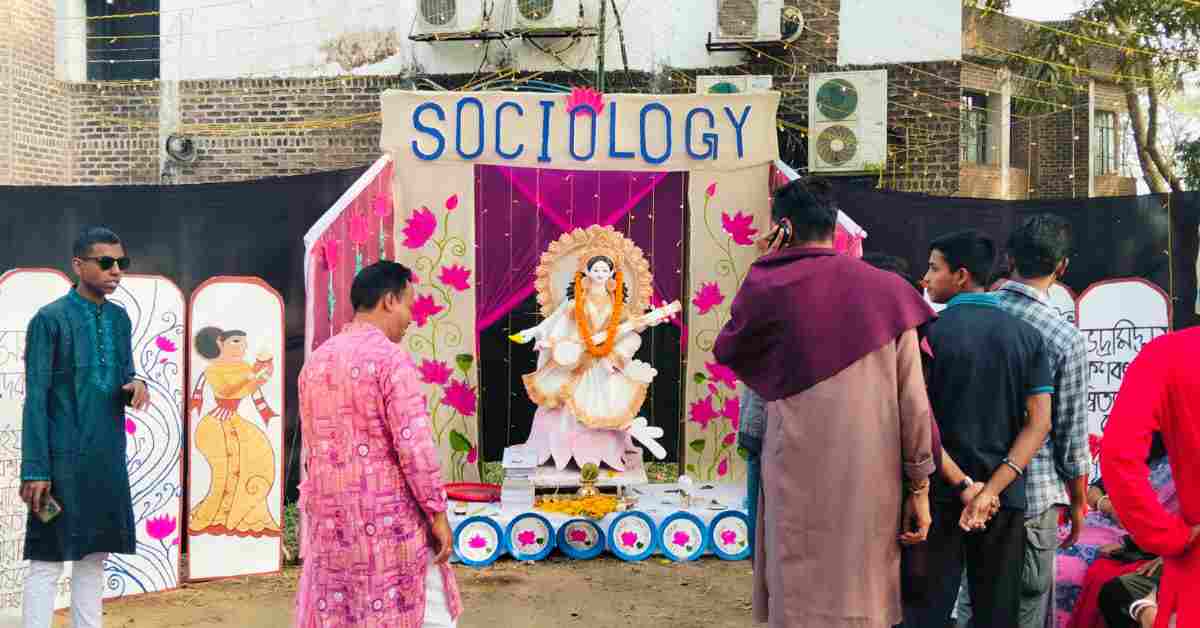আপডেট: ১৫:৫৬, ৬ আগস্ট ২০১৯
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত উপলব্ধির খসড়া
১. রবীন্দ্রনাথ পুরোদস্তুর কবি। নিখাদ। তিনি যখন গদ্য লেখেন, তখনও। গদ্যও যে টিকাটিপ্পনির ভার থেকে মুক্ত হয়ে সকল টিকাটিপ্পনির সারাৎসার নিজের ভেতর ধারণ করে নিজের মতো রোমান্টিকতায় লেখা যায়, তার সবল উদাহরণ তিনি। তার আগে অবনীন্দ্রনাথ, তবে তা কেবল শিল্পের আলোচনায়।
রবীন্দ্রনাথ ‘কোনো কালের কোনো সমাজের’ থাকেন নাই, ফলে তাকে ধারণ করা আজকের ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। দেখানেওয়ালা কৃত্যাচার ছাড়া বলতে গেলে ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নির্বাসিতই, রবীন্দ্রনাথ বাঁচবেন বাংলাদেশে, বাংলাদেশকেও বাঁচাবেন তিনি।
২. রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা পয়েটিক আর রোমান্টিক। তিনি বারবার অনুভব করতে চেয়েছেন ‘সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়’, কিন্তু জাতীয় বিষয়টাই হৃদয়-সম্মিলনের প্রধান বাধা, সেটা টের পান নাই। বলেছেন, মিলবে যে আজ অকূল পানে, তোমার গানে আমার গানে’, সেই গানে গান মেলানোর আকুতি রাজনৈতিক নয়, মানবিক। প্লেটোর মতো রবীন্দ্রনাথও রাষ্ট্র-জাতি -দেশ-ধর্ম সব কিছুর অস্তিত্বের মধ্যেই মানুষের মিলন কল্পনা করেছেন। ’
৩. লালন সরাসরিই জাত আর ধর্মকে অতিক্রম করে মানুষের পরমাত্মিক মিলনকে বাঞ্ছা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাত আর ধর্মের ভেতর দিয়ে। কিন্তু সেই জাত আর ধর্ম জন্মসূত্রে মেনে নেবার দায়ে নয়, নিরন্তর সংঘর্ষে মোকাবিলায় বোঝাপড়ায় কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার। তার সামাজিক সত্তার মানবমুক্তি মিলনের সংকট আর অস্থিরতা :‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি’, আর কবিসত্তার মোক্ষ : ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান’।
৪. রবীন্দ্রনাথের আপনা জমিন ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষকে দার্শনিকভাবে তিনি চিনেছেন হিন্দু আর ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতের মধ্য় দিয়ে। ভারতবর্ষকে (অ)পর ক্ষমতা ও শক্তির থাবা থেকে বাঁচানোর জন্য তারও একটা জাতীয়তাবাদের দরকার পড়েছে। সেই জাতীয়তাবাদ হিন্দু কিবা সনাতন নয়, ব্রাহ্মও নয়, আপাত দৃষ্টিতে সেরকম মনে হলেও সেটা তার শিল্পকর্মে নিয়ত সাংঘর্ষিক রূপেই থেকেছে। হিন্দুত্ব আর বাঙালিত্বের যে নগ্নরূপ তিনি তার গল্প উপন্যাস নাটকে এঁকেছেন, আর কেউ তার ছিটেফোঁটাও করেন নাই।
৫. রবীন্দ্রনাথে পইলা জীবনের ইংরেজ বা ইংরেজিপ্রীতি তার পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। হিন্দু সমাজের জাত-পাত-নানান সংকীর্ণতা এবং বাঙালির স্বভাবের দেউলিয়াপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তার সেই আকর্ষণ ঘটেছিল, সেটা তার সামাজিক সত্তার বোঝাপড়া। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী রূপটাকে যখন স্পষ্টভাবে চিনতে পারেন, তখন জন্ম নেন রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথ, যেখানে ইংরেজ ও সকল বেনিয়াই হলো পরিত্যাজ্য।
৬. রবীন্দ্রনাথ কোনোমতেই মুসলিমবিদ্বেষী নন। শুধু মুসলিম নয়, কোনো ধর্মেরই বিদ্বেষ তার লেখায় নাই। মুসলমান সমাজকে তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু না করাটা তার রবীন্দ্রনাথসুলভ যথার্থ সাহিত্যিক সিদ্ধান্ত। সাহিত্য সমাজের গুণগান করে না, সমাজের অভ্যন্তর রূপ উন্মোচন করাই তার শৈল্পিক লক্ষ্য। নিজ সমাজের (বা ধর্মের) ক্ষেত্রে যা্ তিনি নিঃসংকোচে করতে পারেন, অপর সমাজের ক্ষেত্রে তা কখনোই করতে পারেন না। বা পারলেও তিনি তখন সেই সমাজের কাছে কেমন গ্রহণযোগ্য হবেন?
৭. নজরুলের মতো মুখে না বললেও রবীন্দ্রনাথ ‘কোনো কালের কোনো সমাজের’ থাকেন নাই, ফলে তাকে ধারণ করা আজকের ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। দেখানেওয়ালা কৃত্যাচার ছাড়া বলতে গেলে ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নির্বাসিতই, রবীন্দ্রনাথ বাঁচবেন বাংলাদেশে, বাংলাদেশকেও বাঁচাবেন তিনি।
কেন, কীভাবে, তার আলাপ অন্য একদিন করা যাবে।
শুভাশিস সিনহা, কবি ও নাট্যকার- কাল থেকে যেসব শাখায় পাওয়া যাবে নতুন টাকার নোট
- 'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' গঠনের ঘোষণা
- এক বছরেই শক্তি, ক্ষিপ্রতা জৌলুস হারিয়ে 'হীরা' এখন বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী
- ওয়াহিদ সরদার: গাছ বাঁচাতে লড়ে যাওয়া এক সৈনিক
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিকথা (প্রথম পর্ব)
- এবার ভাইরাস বিরোধী মাস্ক বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলো বাংলাদেশ
- মায়েরখাবারের জন্য ভিক্ষা করছে শিশু
- ২৫ কেজি স্বর্ণ বিক্রি করল বাংলাদেশ ব্যাংক
- ঈদে মিলাদুন্নবী ২০২৩ কত তারিখ
- তালিকা হবে রাজাকারদের