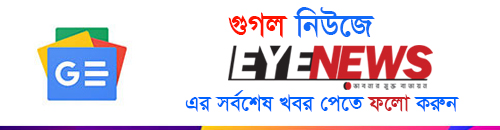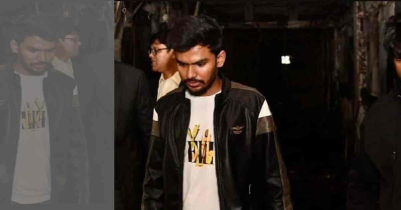প্রকাশিত: ০৮:২১, ৮ মে ২০১৯
আপডেট: ০৯:৩৯, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০
আপডেট: ০৯:৩৯, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০
বুনো ঘাস থেকে যেভাবে ধানের রূপান্তর
কাজী মাহবুব হাসান: এশিয়ার একটি বুনো ঘাস প্রজাতিকে আদি মানুষ রূপান্তর করেছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্যশস্যে - ধান । পুরো এশিয় সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল ধানের উপর ভিত্তি করে - Oryza sativa, যদি আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে হয়, বর্তমানে পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীর এটিই প্রধান খাদ্য। শিকারী – সংগ্রাহক যাযাবর মানুষকে যা একদিন গৃহবাসী কৃষকে রুপান্তরিত করেছিল। ধানের বিবর্তন ইতিহাস বেশ বিতর্কিত, কারণ এশিয়ার বেশ কিছু এলাকাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে এর গৃহস্থীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা স্থল হিসাবে, কিন্তু বিবর্তন জিনতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার বেশ কিছু আবিষ্কার সেই রহস্যটি সমাধান করেছে।
Oryza rufipogon, এশিয়ার যে বুনো ঘাসটি সরাসরিভাবে আমাদের পরিচিত ধান O. sativa প্রজাতির সাথে যুক্ত, সেটি আগাছার মত রুগ্ন একটি উদ্ভিদ, তবে এর লাল বীজটি খাওয়ার উপযোগী, যদিও আধুনিক ধানের চাষ যারা করেন তাদের কাছে এটি আগাছাই। প্রায় ৯০০০ বছর আগে যখন মানুষ প্রথম ধান চাষ করতে শুরু করেছিল, তারা সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে বাছাই করেছে যা তাদের কাছে কাম্য, এবং কয়েক শতাব্দী পরেই উদ্ভিদটি তার বর্তমান রুপ পেয়েছে – আরো শক্তিশালী, বেশী শস্যবীজ উৎপাদনকারী এবং যারা পাকলে শীষের মধ্যেই আটকে থাকে মাটিতে ঝরে পড়ে না, যা বুনো ধানটি করতো তাদের প্রজনন বিস্তারের জন্য।
rufipogon, এর প্রাকৃতিক বিস্তার বেশ বড় আর সে কারণেই ধান কোথায় গৃহস্থীকরণ হয়েছে তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দী দুটি তত্ত্ব আছে, উত্তর ভারতে গঙ্গা উপত্যাকা, চিনের বেশ কিছু এলাকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল ইত্যাদি। তবে গত কয়েক দশকে এই গবেষণার দুটি কেন্দ্র ছিল, ভারত এবং চিন। তাইওয়ানের প্রয়াত বিজ্ঞারী তে-স্যু চ্যাঙ পুরো এশিয়া জুড়েই ষাট ও সত্তরের দশকে বেশ কিছু বুনো ধান সংগ্রহ ও চাষ করেছিলেন, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, এই গৃহস্থী করণের ঘটনা ঘটেছিল উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ চিন অবধি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। হান রাজবংশের ২০০০ বছর আগের তথ্য জানাচ্ছে , দুই ধরনের ধানের পার্থক্য – Keng আর Hsien, বর্তমানে যা পরিচিত যথাক্রমে, japonica (short-grained) ও indica (long-grained) । গবেষণা দেখিয়েছে যে এই দুটি প্রকার তাদের নিজেদের সাথে যতটা না সম্পর্কযুক্ত তার চেয়ে বেশী সম্পর্কযুক্ত বুনো ধানের সাথে।। যা ইঙ্গিত দিচ্ছে দুটি ভিন্ন গৃহস্থীকরণ ঘটনার। অর্থাৎ চিন এবং ভারত।
কিন্তু জিনগতভাবে বেশ ভিন্ন হলেও ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে গৃহপালিত ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিউটেশন sh4, যা মুলত ধানের বীজের ছিটকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করে ( যাকে বলে shattering), japonica আর indica র এই sh4 হুবুহু একরকম, অর্থাৎ তাদের দুটি প্রকারের পূর্বসূরি এক। পরে বিজ্ঞানীরা দেখান যে এই মিউটেশনটির উদ্ভব হয়েছিল প্রথমে japonica য় এবং পরে এটি indica প্রকারে প্রবেশ করেছে। ধানের গৃহপালিত করণ প্রক্রিয়া অন্য জিনগুলোও দেখা গেছে ঠিক এভাবেই দুটি প্রকারে প্রবেশ করেছে। একটি উদহারণ যেমন একটি জিন Rc, যা বীজের উপরের পর্দা বা পেরিকার্প এর রং হালকা করে। কিন্তু এইসব আবিষ্কারগুলো ধান গবেষকদের সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল, কিভাবে জিনগতভাবে বেশ ভিন্ন দুটি প্রকার একই ধরনের মিউটেশন বহন করে, যে মিউটেশনগুলো তাদের চাষাবাদের জন্য উপযোগি করে তোলে। যদি বিতর্কিত তবে অনেক গবেষকই মনে করেন মানুষই এই হাইব্রিডাজেশনের কাজ করেছে ধান গৃহপালিত করার গুরুত্বপূর্ণ ধাপে।
২০১১ সালের একটি গবেষণা দেখায় japonica, গৃহপালিত হয়েছিল প্রথম চিনে, সেখান থেকেই এটি ভারতে প্রবেশ করে, যেখানে কৃষকরা একটি স্থানীয় প্রজাতির সাথে এটিকে হাইব্রিডাইজ করে indica প্রকারটি সৃষ্টি করে। তবে কোনো স্থানীয় ধানটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি ঘটেছিল ধানের গৃহস্থীকরণে সেটি ঘটেছিল চিনে।
কিন্তু চীনের ঠিক কোথায় japonica কে বশে এনেছিল মানুষ – ২০১১ সালে প্রায় ৮০০০ বছর পুরানো ধানের নিদর্শন মেলে পূর্ব চীনের ইয়াংসি নদী উপত্যাকার নীচের অংশে, কিন্তু ২০১২ সালে চীনের জিনতত্ত্ববিদ বিন হান, প্রায় ১৪৪৬ ধরনের ধানে জিন বিশ্লেষণ করে দাবী করেন দুই প্রকার ধানের যে পূর্বসূরি, সেই বুনো ধানটি উৎস পার্ল নদীর উপত্যাকা, তার পক্ষে অবশ্য কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ছিল না। তবে তিনি দাবী করেন এর কারণ পার্ল উপত্যাকায় বাস করা মানুষগুলোর তুলনামূলক দারিদ্র, তারা ইয়াংসি আদিবাসীদের মত ধানের বিশাল মজুত রেখে যায়নি।
[caption id="attachment_3116" align="alignnone" width="743"] ছবিঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত[/caption]
তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো মূলত ইয়াংসি কেন্দ্রিক। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আদি মানুষরা যদিও ধান চাষের চেষ্টা করেছিল, তবে তার খাদ্য ছিল অ্যাকর্ন, ওয়াটার চেষ্টনাট ও মাছ। সেখানেই খণনে বিজ্ঞানীরা দেখেন ৫০০০ আগের সময় থেকে আধুনিক ধানের মত কিছু ধান ক্রমশ দেখতে পাওয়া যায়, যা ক্রমশ তাদের আকার ও গঠন বদেলেছে। আর ধানের আকৃতি যখন একটি স্থিতিশীল রুপ পেয়েছে, খণনে সেই স্তরে আর অ্যাকর্নের দেখা মেলেনি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন প্রাচীন সেই ধানের ডিএনএ উদ্ধার করার জন্য, যার মাধ্যমে আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ মিউটেশনগুলো কখন উদ্ভব হয়েছে সেগুলো শনাক্ত করতে পারবো। বেশ কিছু দিন হলো সেই ধরেনের ডিএনএ কারিগরী দক্ষতা মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে, যেমন মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রে।
তাহলে আপাতত গবেষণা জানাচ্ছে ধানের বিবর্তনের গল্প শুরু হয়েছিল এশিয়ায়, শিকারী সংগ্রহকারী মানুষ প্রায় ৯০০০ বছর আগে, বর্তমান চীনে ইয়াংসি উপত্যাকায় প্রথম বুনো ধানের প্রজাতি Oryza rufipogon চাষ করা শুরু করেছিল, এই প্রজাতিটি বিবর্তিত হয়ে পরিচিত O. sativa প্রজাতিতে। তবে এশিয়ায় যখন ধানের চাষ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, ধানের গৃহস্থীকরণের ( Oryza জিনাসে) আরেকটি পরীক্ষা শুরু করেছিল নাইজার নদী বদ্বীপে আফ্রিকার আদি কৃষকরা, প্রায় ৩০০০ বছর আগে তারা Oryza barthii চাষ করা শুরু করেছিল পরে যা বিবর্তিত হয় O. glaberrima প্রজাতিতে। বর্তমান পৃথিবীতে O. sativa ধানের গুরুত্ব কোনোভাবেই বাড়িয়ে বলা সম্ভব না, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রধান খাদ্য। আফ্রিকান ধান ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি, আফ্রিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ মূলত O. glaberrima । O. sativa আর O. glaberrima সমান্তরাল শস্য গৃহস্থীকরণের উদহারণ, যা ঘটেছিল, দুটি ভিন্ন মহাদেশে। কিন্তু বিবর্তনের কারণ কি ছিল একই সেট জিন?
এশিয়ার কৃষকদের ধানকে গৃহপালিত করার বেশ কয়েক হাজার বছর পর আফ্রিকার কৃষকরাও তাদের নিজেদের একটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছিল, আফ্রিকার সেই ধান Oryza glaberrima, সাধারণ এশিয়ার ধানের মত এত বীজ তৈরী করেনা, যদি ধান আফ্রিকায় কখনোই প্রধান খাদ্য শস্য হতে পারেনি, তবে কিছু স্থানীয় খাদ্যতালিকায় এর একটি ঐতিহাসিক অবস্থান আছে। আফ্রিকান ধানটি এসেছে Oryza barthii নামের একটি বুনো প্রজাতি থেকে, জিনোম বিশ্লেষণ জানাচ্ছে আফ্রিকান ধান একবারই গৃহপালিত হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজার নদীর বদ্বীপে। আর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, আফ্রিকান ধানের মিউটেশন আছে সেই একই জিনগুলোয় যারা শীষ থেকে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করে, এছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও একই রকম।
যদিও আফ্রিকার আর এশিয়ার মানুষ স্বতন্ত্রভাবে হাজার বছরের ব্যবধানে ধানকে চাষাবাদ উপযোগী করেছে, কিন্তু তারা দুটি ধানের জিনোমকেই বদলেছে একই ভাবে।
ষাটের দশকের শুরুতে.. ব্রিসবেসে বিয়ার পান করার সময় ধারণাটি নিয়ে প্রথম ভেবেছিলেন দুই অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী হ্যাল হ্যাচ ও রজার স্ল্যাক। দুজনেই তখন ব্রিসবেনে কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কোম্পানীর ল্যাবে কর্মরত। পাবের সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ করেই পারস্পরিক কৌতুহলে স্থির হয় একটি প্রশ্নে, কিভাবে আখ এত বেশী সুগার তৈরী আর সংরক্ষণ করতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা দুজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার করেন: C4 photosynthetic pathway, যার মাধ্যমে আখসহ উদ্ভিদ জগতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ সদস্য বাতাসের অজৈব কার্বনকে রুপান্তর করে একটি জৈব যৌগে - সুগার বা শর্করা।
তাদের দুজনেরই সালোক সংশ্লেষণের বিকল্প C3 pathway এর কথা জানা ছিল, তারা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা হলো C4 pathway, C3 pathway থেকে অনেক বেশী দক্ষ, কারণ এটি অপেক্ষ কম আলোক শক্তি খরচ করে কার্বনকে সুগারে বন্ধন করতে। আর বাড়তি সুবিধা হিসাবে, C4 ব্যবহারকারী উদ্ভিদদের পানি এবং নাইট্রোজেনও কম লাগে এই প্রক্রিয়াটিকে চালানোর জন্য। অর্থাৎ C4 উদ্ভিদগুলো অনেক অল্পতেই বেশী কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণ শস্য যেমন ভুট্টা বা মেইজ, মিলেট আর শরগামেও C4 pathway খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া, যার উপর পৃথিবী সুবিশাল একটি জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল - সেটি হচ্ছে ধান।
বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেন যদি তারা C3 ধানকে C4 ধানে রুপান্তরিত করতে পারেন, আরো বেশী পরিমান ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে, আর সেটি করার সম্ভব হবে আরো দক্ষ, টেকসই উপায়ে, এমনকি আরো উষ্ণতর, শুষ্ক আর জনবহুল এলাকায়। ফিলিপাইনের nternational Rice Research Institute এ International C4 Rice Consortium (ICRC) এর মতে এধরনের সুপারচার্জড ধান একই পরিমান পানি আর সার ব্যবহার করে বর্তমান C3 ধান অপেক্ষা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশী ফলন দেবে।
২০১৩ সালে IRRI র Applied Photosynthesis and Systems
Modeling Laboratory সাবেক প্রধান ও C4 project এর জনক জন শিহি’র মতে ৬০ মিলিয়ন বছরে এই গ্রহে C3 থেকে C4 এ রুপান্তরের কাজটি বেশ কয়েকবারই করেছে বিবর্তন, যখন উদ্ভিদরা উষ্ণতর, প্রায় শুষ্ক এলাকায় তাদের বসতি গড়েছে। ধানও এমন আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে। শুধু প্রয়োজন আরো দক্ষতর করে তোলা। বিজ্ঞানীরা আসলেই নতুন কিছু করছেন না, শুধুমাত্র প্রকৃতিকে অনুকরণ করছেন পৃথিবীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে। কাজটি করছেন মোট ৯ টি দেশের বিজ্ঞানীদের ২২ টি দল। প্রয়োজনীয় ১২ টি জিনের ৬ টি জিনকে যুক্ত করা হয়েছে এই রুপান্তরের জন্য, তবে এখনও অনেক ধাপই বাকী, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আরো ১৫ বছরের আগে এই কাজটি শেষ হবে না।
ছবিঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত[/caption]
তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো মূলত ইয়াংসি কেন্দ্রিক। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আদি মানুষরা যদিও ধান চাষের চেষ্টা করেছিল, তবে তার খাদ্য ছিল অ্যাকর্ন, ওয়াটার চেষ্টনাট ও মাছ। সেখানেই খণনে বিজ্ঞানীরা দেখেন ৫০০০ আগের সময় থেকে আধুনিক ধানের মত কিছু ধান ক্রমশ দেখতে পাওয়া যায়, যা ক্রমশ তাদের আকার ও গঠন বদেলেছে। আর ধানের আকৃতি যখন একটি স্থিতিশীল রুপ পেয়েছে, খণনে সেই স্তরে আর অ্যাকর্নের দেখা মেলেনি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন প্রাচীন সেই ধানের ডিএনএ উদ্ধার করার জন্য, যার মাধ্যমে আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ মিউটেশনগুলো কখন উদ্ভব হয়েছে সেগুলো শনাক্ত করতে পারবো। বেশ কিছু দিন হলো সেই ধরেনের ডিএনএ কারিগরী দক্ষতা মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে, যেমন মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রে।
তাহলে আপাতত গবেষণা জানাচ্ছে ধানের বিবর্তনের গল্প শুরু হয়েছিল এশিয়ায়, শিকারী সংগ্রহকারী মানুষ প্রায় ৯০০০ বছর আগে, বর্তমান চীনে ইয়াংসি উপত্যাকায় প্রথম বুনো ধানের প্রজাতি Oryza rufipogon চাষ করা শুরু করেছিল, এই প্রজাতিটি বিবর্তিত হয়ে পরিচিত O. sativa প্রজাতিতে। তবে এশিয়ায় যখন ধানের চাষ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, ধানের গৃহস্থীকরণের ( Oryza জিনাসে) আরেকটি পরীক্ষা শুরু করেছিল নাইজার নদী বদ্বীপে আফ্রিকার আদি কৃষকরা, প্রায় ৩০০০ বছর আগে তারা Oryza barthii চাষ করা শুরু করেছিল পরে যা বিবর্তিত হয় O. glaberrima প্রজাতিতে। বর্তমান পৃথিবীতে O. sativa ধানের গুরুত্ব কোনোভাবেই বাড়িয়ে বলা সম্ভব না, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রধান খাদ্য। আফ্রিকান ধান ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি, আফ্রিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ মূলত O. glaberrima । O. sativa আর O. glaberrima সমান্তরাল শস্য গৃহস্থীকরণের উদহারণ, যা ঘটেছিল, দুটি ভিন্ন মহাদেশে। কিন্তু বিবর্তনের কারণ কি ছিল একই সেট জিন?
এশিয়ার কৃষকদের ধানকে গৃহপালিত করার বেশ কয়েক হাজার বছর পর আফ্রিকার কৃষকরাও তাদের নিজেদের একটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছিল, আফ্রিকার সেই ধান Oryza glaberrima, সাধারণ এশিয়ার ধানের মত এত বীজ তৈরী করেনা, যদি ধান আফ্রিকায় কখনোই প্রধান খাদ্য শস্য হতে পারেনি, তবে কিছু স্থানীয় খাদ্যতালিকায় এর একটি ঐতিহাসিক অবস্থান আছে। আফ্রিকান ধানটি এসেছে Oryza barthii নামের একটি বুনো প্রজাতি থেকে, জিনোম বিশ্লেষণ জানাচ্ছে আফ্রিকান ধান একবারই গৃহপালিত হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজার নদীর বদ্বীপে। আর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, আফ্রিকান ধানের মিউটেশন আছে সেই একই জিনগুলোয় যারা শীষ থেকে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করে, এছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও একই রকম।
যদিও আফ্রিকার আর এশিয়ার মানুষ স্বতন্ত্রভাবে হাজার বছরের ব্যবধানে ধানকে চাষাবাদ উপযোগী করেছে, কিন্তু তারা দুটি ধানের জিনোমকেই বদলেছে একই ভাবে।
ষাটের দশকের শুরুতে.. ব্রিসবেসে বিয়ার পান করার সময় ধারণাটি নিয়ে প্রথম ভেবেছিলেন দুই অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী হ্যাল হ্যাচ ও রজার স্ল্যাক। দুজনেই তখন ব্রিসবেনে কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কোম্পানীর ল্যাবে কর্মরত। পাবের সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ করেই পারস্পরিক কৌতুহলে স্থির হয় একটি প্রশ্নে, কিভাবে আখ এত বেশী সুগার তৈরী আর সংরক্ষণ করতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা দুজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার করেন: C4 photosynthetic pathway, যার মাধ্যমে আখসহ উদ্ভিদ জগতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ সদস্য বাতাসের অজৈব কার্বনকে রুপান্তর করে একটি জৈব যৌগে - সুগার বা শর্করা।
তাদের দুজনেরই সালোক সংশ্লেষণের বিকল্প C3 pathway এর কথা জানা ছিল, তারা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা হলো C4 pathway, C3 pathway থেকে অনেক বেশী দক্ষ, কারণ এটি অপেক্ষ কম আলোক শক্তি খরচ করে কার্বনকে সুগারে বন্ধন করতে। আর বাড়তি সুবিধা হিসাবে, C4 ব্যবহারকারী উদ্ভিদদের পানি এবং নাইট্রোজেনও কম লাগে এই প্রক্রিয়াটিকে চালানোর জন্য। অর্থাৎ C4 উদ্ভিদগুলো অনেক অল্পতেই বেশী কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণ শস্য যেমন ভুট্টা বা মেইজ, মিলেট আর শরগামেও C4 pathway খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া, যার উপর পৃথিবী সুবিশাল একটি জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল - সেটি হচ্ছে ধান।
বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেন যদি তারা C3 ধানকে C4 ধানে রুপান্তরিত করতে পারেন, আরো বেশী পরিমান ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে, আর সেটি করার সম্ভব হবে আরো দক্ষ, টেকসই উপায়ে, এমনকি আরো উষ্ণতর, শুষ্ক আর জনবহুল এলাকায়। ফিলিপাইনের nternational Rice Research Institute এ International C4 Rice Consortium (ICRC) এর মতে এধরনের সুপারচার্জড ধান একই পরিমান পানি আর সার ব্যবহার করে বর্তমান C3 ধান অপেক্ষা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশী ফলন দেবে।
২০১৩ সালে IRRI র Applied Photosynthesis and Systems
Modeling Laboratory সাবেক প্রধান ও C4 project এর জনক জন শিহি’র মতে ৬০ মিলিয়ন বছরে এই গ্রহে C3 থেকে C4 এ রুপান্তরের কাজটি বেশ কয়েকবারই করেছে বিবর্তন, যখন উদ্ভিদরা উষ্ণতর, প্রায় শুষ্ক এলাকায় তাদের বসতি গড়েছে। ধানও এমন আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে। শুধু প্রয়োজন আরো দক্ষতর করে তোলা। বিজ্ঞানীরা আসলেই নতুন কিছু করছেন না, শুধুমাত্র প্রকৃতিকে অনুকরণ করছেন পৃথিবীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে। কাজটি করছেন মোট ৯ টি দেশের বিজ্ঞানীদের ২২ টি দল। প্রয়োজনীয় ১২ টি জিনের ৬ টি জিনকে যুক্ত করা হয়েছে এই রুপান্তরের জন্য, তবে এখনও অনেক ধাপই বাকী, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আরো ১৫ বছরের আগে এই কাজটি শেষ হবে না।
 ছবিঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত[/caption]
তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো মূলত ইয়াংসি কেন্দ্রিক। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আদি মানুষরা যদিও ধান চাষের চেষ্টা করেছিল, তবে তার খাদ্য ছিল অ্যাকর্ন, ওয়াটার চেষ্টনাট ও মাছ। সেখানেই খণনে বিজ্ঞানীরা দেখেন ৫০০০ আগের সময় থেকে আধুনিক ধানের মত কিছু ধান ক্রমশ দেখতে পাওয়া যায়, যা ক্রমশ তাদের আকার ও গঠন বদেলেছে। আর ধানের আকৃতি যখন একটি স্থিতিশীল রুপ পেয়েছে, খণনে সেই স্তরে আর অ্যাকর্নের দেখা মেলেনি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন প্রাচীন সেই ধানের ডিএনএ উদ্ধার করার জন্য, যার মাধ্যমে আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ মিউটেশনগুলো কখন উদ্ভব হয়েছে সেগুলো শনাক্ত করতে পারবো। বেশ কিছু দিন হলো সেই ধরেনের ডিএনএ কারিগরী দক্ষতা মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে, যেমন মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রে।
তাহলে আপাতত গবেষণা জানাচ্ছে ধানের বিবর্তনের গল্প শুরু হয়েছিল এশিয়ায়, শিকারী সংগ্রহকারী মানুষ প্রায় ৯০০০ বছর আগে, বর্তমান চীনে ইয়াংসি উপত্যাকায় প্রথম বুনো ধানের প্রজাতি Oryza rufipogon চাষ করা শুরু করেছিল, এই প্রজাতিটি বিবর্তিত হয়ে পরিচিত O. sativa প্রজাতিতে। তবে এশিয়ায় যখন ধানের চাষ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, ধানের গৃহস্থীকরণের ( Oryza জিনাসে) আরেকটি পরীক্ষা শুরু করেছিল নাইজার নদী বদ্বীপে আফ্রিকার আদি কৃষকরা, প্রায় ৩০০০ বছর আগে তারা Oryza barthii চাষ করা শুরু করেছিল পরে যা বিবর্তিত হয় O. glaberrima প্রজাতিতে। বর্তমান পৃথিবীতে O. sativa ধানের গুরুত্ব কোনোভাবেই বাড়িয়ে বলা সম্ভব না, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রধান খাদ্য। আফ্রিকান ধান ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি, আফ্রিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ মূলত O. glaberrima । O. sativa আর O. glaberrima সমান্তরাল শস্য গৃহস্থীকরণের উদহারণ, যা ঘটেছিল, দুটি ভিন্ন মহাদেশে। কিন্তু বিবর্তনের কারণ কি ছিল একই সেট জিন?
এশিয়ার কৃষকদের ধানকে গৃহপালিত করার বেশ কয়েক হাজার বছর পর আফ্রিকার কৃষকরাও তাদের নিজেদের একটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছিল, আফ্রিকার সেই ধান Oryza glaberrima, সাধারণ এশিয়ার ধানের মত এত বীজ তৈরী করেনা, যদি ধান আফ্রিকায় কখনোই প্রধান খাদ্য শস্য হতে পারেনি, তবে কিছু স্থানীয় খাদ্যতালিকায় এর একটি ঐতিহাসিক অবস্থান আছে। আফ্রিকান ধানটি এসেছে Oryza barthii নামের একটি বুনো প্রজাতি থেকে, জিনোম বিশ্লেষণ জানাচ্ছে আফ্রিকান ধান একবারই গৃহপালিত হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজার নদীর বদ্বীপে। আর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, আফ্রিকান ধানের মিউটেশন আছে সেই একই জিনগুলোয় যারা শীষ থেকে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করে, এছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও একই রকম।
যদিও আফ্রিকার আর এশিয়ার মানুষ স্বতন্ত্রভাবে হাজার বছরের ব্যবধানে ধানকে চাষাবাদ উপযোগী করেছে, কিন্তু তারা দুটি ধানের জিনোমকেই বদলেছে একই ভাবে।
ষাটের দশকের শুরুতে.. ব্রিসবেসে বিয়ার পান করার সময় ধারণাটি নিয়ে প্রথম ভেবেছিলেন দুই অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী হ্যাল হ্যাচ ও রজার স্ল্যাক। দুজনেই তখন ব্রিসবেনে কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কোম্পানীর ল্যাবে কর্মরত। পাবের সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ করেই পারস্পরিক কৌতুহলে স্থির হয় একটি প্রশ্নে, কিভাবে আখ এত বেশী সুগার তৈরী আর সংরক্ষণ করতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা দুজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার করেন: C4 photosynthetic pathway, যার মাধ্যমে আখসহ উদ্ভিদ জগতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ সদস্য বাতাসের অজৈব কার্বনকে রুপান্তর করে একটি জৈব যৌগে - সুগার বা শর্করা।
তাদের দুজনেরই সালোক সংশ্লেষণের বিকল্প C3 pathway এর কথা জানা ছিল, তারা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা হলো C4 pathway, C3 pathway থেকে অনেক বেশী দক্ষ, কারণ এটি অপেক্ষ কম আলোক শক্তি খরচ করে কার্বনকে সুগারে বন্ধন করতে। আর বাড়তি সুবিধা হিসাবে, C4 ব্যবহারকারী উদ্ভিদদের পানি এবং নাইট্রোজেনও কম লাগে এই প্রক্রিয়াটিকে চালানোর জন্য। অর্থাৎ C4 উদ্ভিদগুলো অনেক অল্পতেই বেশী কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণ শস্য যেমন ভুট্টা বা মেইজ, মিলেট আর শরগামেও C4 pathway খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া, যার উপর পৃথিবী সুবিশাল একটি জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল - সেটি হচ্ছে ধান।
বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেন যদি তারা C3 ধানকে C4 ধানে রুপান্তরিত করতে পারেন, আরো বেশী পরিমান ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে, আর সেটি করার সম্ভব হবে আরো দক্ষ, টেকসই উপায়ে, এমনকি আরো উষ্ণতর, শুষ্ক আর জনবহুল এলাকায়। ফিলিপাইনের nternational Rice Research Institute এ International C4 Rice Consortium (ICRC) এর মতে এধরনের সুপারচার্জড ধান একই পরিমান পানি আর সার ব্যবহার করে বর্তমান C3 ধান অপেক্ষা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশী ফলন দেবে।
২০১৩ সালে IRRI র Applied Photosynthesis and Systems
Modeling Laboratory সাবেক প্রধান ও C4 project এর জনক জন শিহি’র মতে ৬০ মিলিয়ন বছরে এই গ্রহে C3 থেকে C4 এ রুপান্তরের কাজটি বেশ কয়েকবারই করেছে বিবর্তন, যখন উদ্ভিদরা উষ্ণতর, প্রায় শুষ্ক এলাকায় তাদের বসতি গড়েছে। ধানও এমন আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে। শুধু প্রয়োজন আরো দক্ষতর করে তোলা। বিজ্ঞানীরা আসলেই নতুন কিছু করছেন না, শুধুমাত্র প্রকৃতিকে অনুকরণ করছেন পৃথিবীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে। কাজটি করছেন মোট ৯ টি দেশের বিজ্ঞানীদের ২২ টি দল। প্রয়োজনীয় ১২ টি জিনের ৬ টি জিনকে যুক্ত করা হয়েছে এই রুপান্তরের জন্য, তবে এখনও অনেক ধাপই বাকী, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আরো ১৫ বছরের আগে এই কাজটি শেষ হবে না।
ছবিঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত[/caption]
তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো মূলত ইয়াংসি কেন্দ্রিক। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আদি মানুষরা যদিও ধান চাষের চেষ্টা করেছিল, তবে তার খাদ্য ছিল অ্যাকর্ন, ওয়াটার চেষ্টনাট ও মাছ। সেখানেই খণনে বিজ্ঞানীরা দেখেন ৫০০০ আগের সময় থেকে আধুনিক ধানের মত কিছু ধান ক্রমশ দেখতে পাওয়া যায়, যা ক্রমশ তাদের আকার ও গঠন বদেলেছে। আর ধানের আকৃতি যখন একটি স্থিতিশীল রুপ পেয়েছে, খণনে সেই স্তরে আর অ্যাকর্নের দেখা মেলেনি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন প্রাচীন সেই ধানের ডিএনএ উদ্ধার করার জন্য, যার মাধ্যমে আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ মিউটেশনগুলো কখন উদ্ভব হয়েছে সেগুলো শনাক্ত করতে পারবো। বেশ কিছু দিন হলো সেই ধরেনের ডিএনএ কারিগরী দক্ষতা মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে, যেমন মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রে।
তাহলে আপাতত গবেষণা জানাচ্ছে ধানের বিবর্তনের গল্প শুরু হয়েছিল এশিয়ায়, শিকারী সংগ্রহকারী মানুষ প্রায় ৯০০০ বছর আগে, বর্তমান চীনে ইয়াংসি উপত্যাকায় প্রথম বুনো ধানের প্রজাতি Oryza rufipogon চাষ করা শুরু করেছিল, এই প্রজাতিটি বিবর্তিত হয়ে পরিচিত O. sativa প্রজাতিতে। তবে এশিয়ায় যখন ধানের চাষ ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, ধানের গৃহস্থীকরণের ( Oryza জিনাসে) আরেকটি পরীক্ষা শুরু করেছিল নাইজার নদী বদ্বীপে আফ্রিকার আদি কৃষকরা, প্রায় ৩০০০ বছর আগে তারা Oryza barthii চাষ করা শুরু করেছিল পরে যা বিবর্তিত হয় O. glaberrima প্রজাতিতে। বর্তমান পৃথিবীতে O. sativa ধানের গুরুত্ব কোনোভাবেই বাড়িয়ে বলা সম্ভব না, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রধান খাদ্য। আফ্রিকান ধান ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি, আফ্রিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ মূলত O. glaberrima । O. sativa আর O. glaberrima সমান্তরাল শস্য গৃহস্থীকরণের উদহারণ, যা ঘটেছিল, দুটি ভিন্ন মহাদেশে। কিন্তু বিবর্তনের কারণ কি ছিল একই সেট জিন?
এশিয়ার কৃষকদের ধানকে গৃহপালিত করার বেশ কয়েক হাজার বছর পর আফ্রিকার কৃষকরাও তাদের নিজেদের একটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছিল, আফ্রিকার সেই ধান Oryza glaberrima, সাধারণ এশিয়ার ধানের মত এত বীজ তৈরী করেনা, যদি ধান আফ্রিকায় কখনোই প্রধান খাদ্য শস্য হতে পারেনি, তবে কিছু স্থানীয় খাদ্যতালিকায় এর একটি ঐতিহাসিক অবস্থান আছে। আফ্রিকান ধানটি এসেছে Oryza barthii নামের একটি বুনো প্রজাতি থেকে, জিনোম বিশ্লেষণ জানাচ্ছে আফ্রিকান ধান একবারই গৃহপালিত হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজার নদীর বদ্বীপে। আর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, আফ্রিকান ধানের মিউটেশন আছে সেই একই জিনগুলোয় যারা শীষ থেকে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করে, এছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও একই রকম।
যদিও আফ্রিকার আর এশিয়ার মানুষ স্বতন্ত্রভাবে হাজার বছরের ব্যবধানে ধানকে চাষাবাদ উপযোগী করেছে, কিন্তু তারা দুটি ধানের জিনোমকেই বদলেছে একই ভাবে।
ষাটের দশকের শুরুতে.. ব্রিসবেসে বিয়ার পান করার সময় ধারণাটি নিয়ে প্রথম ভেবেছিলেন দুই অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী হ্যাল হ্যাচ ও রজার স্ল্যাক। দুজনেই তখন ব্রিসবেনে কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কোম্পানীর ল্যাবে কর্মরত। পাবের সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ করেই পারস্পরিক কৌতুহলে স্থির হয় একটি প্রশ্নে, কিভাবে আখ এত বেশী সুগার তৈরী আর সংরক্ষণ করতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা দুজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার করেন: C4 photosynthetic pathway, যার মাধ্যমে আখসহ উদ্ভিদ জগতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ সদস্য বাতাসের অজৈব কার্বনকে রুপান্তর করে একটি জৈব যৌগে - সুগার বা শর্করা।
তাদের দুজনেরই সালোক সংশ্লেষণের বিকল্প C3 pathway এর কথা জানা ছিল, তারা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা হলো C4 pathway, C3 pathway থেকে অনেক বেশী দক্ষ, কারণ এটি অপেক্ষ কম আলোক শক্তি খরচ করে কার্বনকে সুগারে বন্ধন করতে। আর বাড়তি সুবিধা হিসাবে, C4 ব্যবহারকারী উদ্ভিদদের পানি এবং নাইট্রোজেনও কম লাগে এই প্রক্রিয়াটিকে চালানোর জন্য। অর্থাৎ C4 উদ্ভিদগুলো অনেক অল্পতেই বেশী কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণ শস্য যেমন ভুট্টা বা মেইজ, মিলেট আর শরগামেও C4 pathway খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া, যার উপর পৃথিবী সুবিশাল একটি জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল - সেটি হচ্ছে ধান।
বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেন যদি তারা C3 ধানকে C4 ধানে রুপান্তরিত করতে পারেন, আরো বেশী পরিমান ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে, আর সেটি করার সম্ভব হবে আরো দক্ষ, টেকসই উপায়ে, এমনকি আরো উষ্ণতর, শুষ্ক আর জনবহুল এলাকায়। ফিলিপাইনের nternational Rice Research Institute এ International C4 Rice Consortium (ICRC) এর মতে এধরনের সুপারচার্জড ধান একই পরিমান পানি আর সার ব্যবহার করে বর্তমান C3 ধান অপেক্ষা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশী ফলন দেবে।
২০১৩ সালে IRRI র Applied Photosynthesis and Systems
Modeling Laboratory সাবেক প্রধান ও C4 project এর জনক জন শিহি’র মতে ৬০ মিলিয়ন বছরে এই গ্রহে C3 থেকে C4 এ রুপান্তরের কাজটি বেশ কয়েকবারই করেছে বিবর্তন, যখন উদ্ভিদরা উষ্ণতর, প্রায় শুষ্ক এলাকায় তাদের বসতি গড়েছে। ধানও এমন আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে। শুধু প্রয়োজন আরো দক্ষতর করে তোলা। বিজ্ঞানীরা আসলেই নতুন কিছু করছেন না, শুধুমাত্র প্রকৃতিকে অনুকরণ করছেন পৃথিবীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে। কাজটি করছেন মোট ৯ টি দেশের বিজ্ঞানীদের ২২ টি দল। প্রয়োজনীয় ১২ টি জিনের ৬ টি জিনকে যুক্ত করা হয়েছে এই রুপান্তরের জন্য, তবে এখনও অনেক ধাপই বাকী, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আরো ১৫ বছরের আগে এই কাজটি শেষ হবে না। আরও পড়ুন
জাতীয় বিভাগের সর্বাধিক পঠিত
- কাল থেকে যেসব শাখায় পাওয়া যাবে নতুন টাকার নোট
- 'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' গঠনের ঘোষণা
- এক বছরেই শক্তি, ক্ষিপ্রতা জৌলুস হারিয়ে 'হীরা' এখন বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী
- ওয়াহিদ সরদার: গাছ বাঁচাতে লড়ে যাওয়া এক সৈনিক
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিকথা (প্রথম পর্ব)
- এবার ভাইরাস বিরোধী মাস্ক বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলো বাংলাদেশ
- মায়েরখাবারের জন্য ভিক্ষা করছে শিশু
- ২৫ কেজি স্বর্ণ বিক্রি করল বাংলাদেশ ব্যাংক
- ঈদে মিলাদুন্নবী ২০২৩ কত তারিখ
- তালিকা হবে রাজাকারদের
সর্বশেষ
জনপ্রিয়