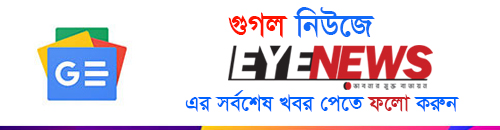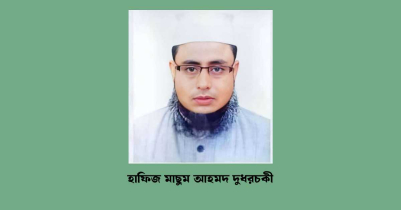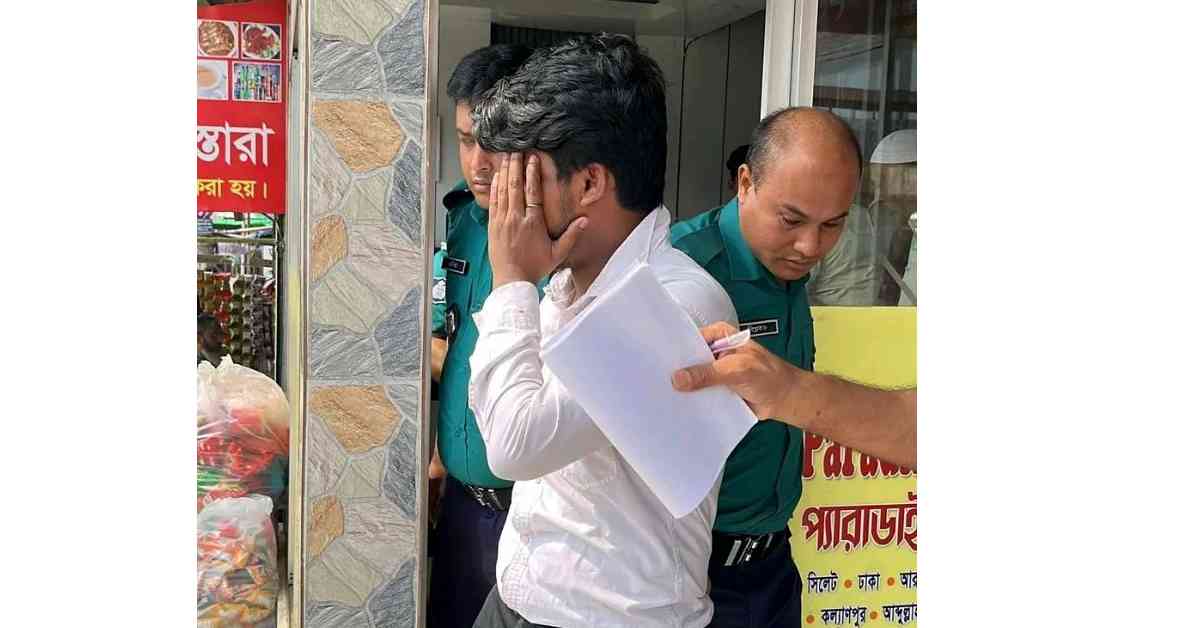সাইফুর রহমান তুহিন
বাংলাদেশের সংবাদপত্রের হারানো সুদিন ও বর্তমান বাস্তবতা

বাংলাদেশে ছাপা হওয়া নানান পত্রিয়া
যতোদূর মনে পড়ে, পত্রিকা পাঠে আমার হাতেখড়ি ক্লাস ফোরে পড়ার সময়। সময়টা আশির দশকের মাঝামাঝি। চিকিৎসক বাবা যে ফার্মেসিতে বসতেন সেখানে অধুনালুপ্ত ‘বাংলার বাণী’ রাখা হতো বলে এটিই হয়ে আছে আমার পড়া প্রথম জাতীয় দৈনিক পত্রিকা।
পর্যায়ক্রমে পরিচয় ঘটে তখনকার নাম্বার ওয়ান পত্রিকা ‘দৈনিক ইত্তেফাক’, সরকারি মালিকানাধীন ‘দৈনিক বাংলা’, ‘দৈনিক সংবাদ’, ‘দৈনিক খবর’ (অধুনালুপ্ত), ‘দৈনিক ইনকিলাব’ প্রভৃতির সাথে। আর ইংরেজি পত্রিকা তখন না পড়লেও ‘দ্য বাংলাদেশ অবজারভার’, ‘দ্য বাংলাদেশ টাইমস’ (অধুনালুপ্ত), ‘দ্য নিউ নেশন’ প্রভৃতির নাম জানতাম। এর মধ্যে একটু আলাদা করে বলতে হবে ইনকিলাবের কথা। বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়ায় এক্সক্লুসিভ স্পোর্টস রিপোর্টিংয়ের পথিকৃত বলা যায় এটিকে। আর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র দাপট ছিল দৈনিক বাংলা গ্রুপের অধুনালুপ্ত ‘বিচিত্রা’র ।
এর পাশাপাশি ইত্তেফাক গ্রুপের প্রকাশনা ‘সাপ্তাহিক রোববার’-এর পাঠকসংখ্যাও কম ছিল না। অধুনালুপ্ত আরেকটি সাপ্তাহিক ‘ছুটি’রও পাঠকপ্রিয়তা ছিল। শফিক রেহমান সম্পাদিত ‘সাপ্তাহিক যায়যায়দিন’ অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠকনন্দিত হলেও বেশি নির্ভীক রিপোর্টিং করতে গিয়ে তৎকালীন এরশাদ সরকারের রোষানলে পড়ে যায়। পত্রিকা
বন্ধ করে দেশত্যাগ করতে হয় সম্পাদক শফিক রেহমানকে। আর আশির দশকের শেষদিকে এসে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইনকিলাব গ্রুপের সহযোগী প্রকাশনা ‘সাপ্তাহিক পূর্ণিমা’।
উপরের বর্ণনায় আশির দশকের প্রিন্ট মিডিয়া সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। আসলে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে মিডিয়া বলতে প্রিন্ট মিডিয়াকেই বুঝাতো যার কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্বল্পতা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল বিটিভি, রেডিওতে বিবিসি বাংলা সার্ভিস, ভয়েস অব আমেরিকা, জার্মান রেডিওর বাংলা সার্ভিস (ডয়েচে ভ্যালে)- ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলতে বুঝাতো মূলত: এগুলোকেই। এই কারণে সংবাদপত্র আর সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ম্যাগাজিনের জনপ্রিয়তা ছিলো আকাশচুম্বী। শিক্ষিত প্রতিটি ঘরের ড্রইংরুমের বুকশেলফ কিংবা টেবিল র্যাকে দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি শোভা পেতো সাপ্তাহিক বিচিত্রা, রোববার, পূর্ণিমা প্রভৃতি। প্রতি রোজার ঈদে এসব সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বের করতো ঢাউস সাইজের ঈদ সংখ্যা। এতে স্থান পেতো দেশসেরা লেখকদের লেখা গল্প ও উপন্যাস থেকে শুরু করে ভ্রমণ কাহিনি, স্মৃতিকথা, মুখরোচক রান্নার রেসিপিসহ অনেক কিছু। এখনো মনে আছে পবিত্র রমজান মাস এলেই সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলোর ঈদ সংখ্যার জন্য পাঠকরা কতোটা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন। তরুণ বয়সে আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। বিশেষ করে সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ও সাপ্তাহিক রোববারের ঈদ সংখ্যা ছাড়া ঈদের সবকিছুকেই যেনো অর্থহীন মনে হতো।
আশির দশকের একেবারে শেষভাগে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক এরশাদের পতন এবং একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রায় এক দশক পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি। এরও কয়েকমাস পর দুই মেরুর দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যকার অভূতপূর্ব ঐক্যমত্যের মাধ্যমে (সম্ভবত: প্রথম ও শেষবার) দেশে পুন:প্রবর্তিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে থাকে গোটা দেশজুড়ে। আর এই অনুকূল পরিবেশের সুবাদে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে রীতিমতো একটি বিপ্লব ঘটে যায় দেশের মিডিয়া অঙ্গনে। এরশাদ আমলে দেশছাড়া সাংবাদিক শফিক রেহমান দেশে ফিরে তার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পুন:প্রকাশ করেন এবং রাতারাতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যায় এটি। এর পাশাপাশি বেরুতে থাকে একের পর এক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা।
এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘দৈনিক আজকের কাগজ’, ‘দৈনিক ভোরের কাগজ’, ‘দৈনিক জনকন্ঠ’, ‘দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা’, ‘দৈনিক মানবজমিন’, ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য ডেইলি স্টার’, ‘দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট (বর্তমানে বন্ধ) প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে বাজারে এসেই বেশ আলোড়ন তোলে ‘দৈনিক প্রথম আলো’। খুব তাড়াতাড়িই প্রচার সংখ্যার বিচারে ইত্তেফাককে ছাড়িয়ে দেশের এক নম্বর বাংলা দৈনিক হয়ে যায় এটি যা এখনো বহাল আছে। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে বের হওয়া ‘সাপ্তাহিক ২০০০’ এবং ‘পাক্ষিক অন্যদিন’ ম্যাগাজিন দুটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায়। বিশেষ করে পাক্ষিক অন্যদিনের কথা আলাদা করে না বললেই নয়। লাইফস্টাইল, ফ্যাশন, রান্নাবান্না এবং বিশেষ করে ভ্রমণ বিষয়ে তাদের ব্যতিক্রমী সব আয়োজনের কথা এখনো অনেক পাঠক ভুলতে পারেননি। এটির মধ্যে পশ্চিম বাংলার দারুণ জনপ্রিয় ফ্যামিলি ম্যাগাজিন ‘সানন্দা’র কিছুটা ছায়া দেখা যেতো। অন্যদিন তাদের ঈদ সংখ্যায় যেভাবে পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলার সেরা লেখকদের লেখার সমাহার ঘটাতো তা ছিলো এককথায় দুর্দান্ত।
এবার বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এই সময়ে আমরা পেয়েছি আরও কিছু দৈনিক পত্রিকা যার মধ্যে ইল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘দৈনিক যুগান্তর’, ‘দৈনিক আমার দেশ’ (বর্তমানে বন্ধ), ‘দৈনিক নয়া দিগন্ত’, ‘দৈনিক সমকাল’, শফিক রেহমান সম্পাদিত ‘দৈনিক যায়যায়দিন’, ‘দৈনিক কালের কন্ঠ’, ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য নিউ এইজ’,‘ডেইলি সান’, ‘দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’ প্রভৃতি। তবে এর মধ্যে আলাদাভাবে বলতে হবে দৈনিক যায়যায়দিনের কথা। পাঠকদের বিরামহীন চাপের প্রেক্ষিতে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের দিকে সাপ্তাহিক যায়যায়দিনকে দৈনিকে রূপান্তর করা হয়। বাজারে এসেই একেবারে হৈ-চৈ ফেলে দেয় পত্রিকাটি।
বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সপ্তাহের সাতদিন সাতটি ম্যাগাজিন মূল পত্রিকার সাথে দেওয়া ছিলো রীতিমতো যুগান্তকারী এক ঘটনা। মূল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ম্যাগাজিনেও এতো বেশি তথ্যের সমাহার থাকতো যে, একজন ছাত্র কিংবা চাকরিজীবীর পক্ষে গভীর রাত পর্যন্ত পড়েও সবকিছু শেষ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু মালিকপক্ষের সাথে বিরোধের জের ধরে মাস ছয়েকের মাথায় যায়যায়দিন থেকে বিদায় ঘটে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শফিক রেহমানের। শুধু সম্পাদক নন, আরও অনেক সিনিয়র সংবাদিকেরও চাকরি চলে যায়। এখন শুধুই নামকাওয়াস্তে টিকে আছে পত্রিকাটি। এর পাশাপাশি আম-ছালা দুটোই যাওয়ার মতো বিলুপ্তি ঘটে সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের।
এছাড়া ‘মিডিয়া ওয়াচ’ নামে সৃজনশীল একটি সাপ্তাহিক ২০০৮ সালে বাজারে এসে জনপ্রিয়তা পায়। নামের সাথে সাদৃশ্য রেখে সাপ্তাহিকটি আগের এক সপ্তাহে দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পরিবেশিত সংবাদকে আতশী কাঁচের নিচে ফেলে সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করতো। সাংবাদিক সমাজ বিশেষ করে নবীন সাংবাদিকদের কাছে এটির বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু বছরখানেক প্রকাশ হওয়ার পরই ক্রমান্বয়ে অনিয়মিত হতে হতে একসময় বিলুপ্তি ঘটে পত্রিকাটির।
সবশেষে আসা যাক বর্তমান সময়ের প্রিন্ট মিডিয়ার প্রসঙ্গে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল- এই ১৬টি বছর ছিল সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়ার স্বর্ণযুগ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূলে থাকা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুসময়, দুটি কারণেই ঐ ১৬ বছরে প্রিন্ট মিডিয়া খুব ভালো সময় কাটিয়েছে। তবে সবকিছু পাল্টে যেতে শুরু করে ২০০৭ সালের বহুল আলোচিত ‘ওয়ান-ইলেভেন’-এর পর থেকে। একে একে হারিয়ে যেতে থাকে পুরনো অনেক পত্রিকা । যে বিষয়টি সবচেয়ে অবাক হওয়ার মতো তা হলো দেশে এখন আর কোনো ভালো সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক ম্যাগাজিন নেই। তুমুল জনপ্রিয় সাপ্তাহিক যায়যায়দিন তো ২০০৬ সালেই হারিয়ে গেছে, এর পাশাপাশি শুধুই স্মৃতি হয়ে গেছে সাপ্তাহিক ২০০০ এবং পাক্ষিক অন্যদিনের মতো ম্যাগাজিনও। যেসব দৈনিক পত্রিকা টিকে আছে সেগুলোও আগের জৌলুস হারিয়েছে অনেকখানি।
প্রথম আলো, কালের কন্ঠ, ডেইলি স্টার, ডেইলি সান, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের মতো আর্থিকভাবে তুলনামূলক সচ্ছল পত্রিকাও অনেক কাটছাঁট করে খরচ সাশ্রয়ে ব্যস্ত। আর এর প্রভাব পড়েছে সংবাদপত্র ব্যবসায়েও। দেশের বিভিন্ন শহরে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন স্টলের সংখ্যা এখন একেবারেই নগণ্য। এই পেশায় দীর্ঘদিন জড়িত থাকা অনেকেই চলে গেছেন অন্য পেশায়। অনেকেই সবকিছুর পেছনে তথ্যপ্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটকে দায়ী করে থাকেন । হ্যাঁ, কথাটি অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতিষ্ঠিত সব দৈনিক পত্রিকারই অনলাইন বা ইন্টারনেট সংস্করণ আছে। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে আবির্ভাব ঘটেছে বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম, বাংলানিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম, রাইজিংবিডি ডটকম, বাংলা ট্রিবিউন, জাগোনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ঢাকা পোস্ট, সকাল সন্ধ্যা প্রভৃতি অনলাইন নিউজ পোর্টালের। এছাড়াও ঢাকার বাইরে জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছে অনেক অনলাইন পত্রিকা যেগুলোর অধিকাংশই পরিচালিত হচ্ছে অদক্ষ লোকদের দ্বারা। এসব পত্রিকার পক্ষে পাঠকের আস্থা অর্জন করা খুবই কঠিন এবং বাস্তবে তা দেখাও যায় না।
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনলাইন পত্রিকা অনেক জনপ্রিয় হয়েছে এটা সত্যি। তবে মানসম্পন্ন অনলাইন পত্রিকার সংখ্যা যে একেবারেই হাতেগোণা তা যেকোনো অনুসন্ধানী পাঠকই বুঝতে পারেন। অথচ অনলাইন পত্রিকার প্রকাশ করা এবং পরিচালনার ব্যয় কাগজে ছাপা পত্রিকার চেয়ে অনেক কম। তারপরও ভালো অনলাইন পত্রিকার সংখ্যা এতো কম হওয়াটা উৎসাহী পাঠক বিশেষ করে তরুণ পাঠকদের জন্য ভালো কিছু নয়। সচেতন পাঠকরা চান যে, একসময় কাগজে ছাপা পত্রিকাগুলোর মধ্যে যেরকম তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা ছিলো তা হোক অনলাইন পত্রিকাগুলোর মধ্যেও। আর কাগজে ছাপা পত্রিকা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা তা সময়ই বলে দেবে।
তবে পাঠকের আস্থা অর্জন করতে হলে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর গুণগত মানের আরও উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারেরও কিছু দায়িত্ব আছে। আমাদের দেশে সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ এখনো খুব সীমিত। এটি অবশ্যই আরও বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) যদি ছয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালিয়ে যেতে পারে তাহলে সাংবাদিকতায় এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে সমস্যা কোথায়? এটি করতে পারলে গোটা দেশে সদ্য গ্র্যাজুয়েশন করা একজন তরুণ-তরূণী প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেই এই পেশায় আসতে পারবেন। প্রতিবেশী ভারতে এমন সুযোগ অনেক আগে থেকেই আছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত সাংবাদিকতার সুযোগ দেওয়াটা এখন সময়ের দাবি। সরকারের যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনাকে দেখতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।
এ বিষয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের একটি অমর উক্তি উল্লেখ করতে হয়। তিনি একবার বলেছিলেন, “সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটি অলীক কল্পনা মাত্র।” এই ধ্রুব সত্যটি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এবং আগামী দিনের নির্বাচিত সরকার যতো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে ততোই সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার জন্য মঙ্গল।

লেখক : সাইফুর রহমান তুহিন, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও ফিচার লেখক
- বাংলাদেশে শিশু শ্রম: কারণ ও করণীয়
- ২০২৩ সালে কী সত্যিই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসছে?
- পনেরো আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক দ্বন্ধ
মোশতাক বললেও মন্ত্রীদের কেউ সেদিন বঙ্গবন্ধুর লাশের সঙ্গে যায়নি! - করোনা যেভাবে চিকিৎসকদের শ্রেণীচ্যুত করলো
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সমস্যা এবং সম্ভাবনা
- ফিলিস্তিনে প্রাণ হারাচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কুকুর স্থানান্তরকরণ ও ভবিষ্যৎ
- শরীফার গল্প পড়তে আমাদের এতো কেন সমস্যা?
- মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী গণমাধ্যমের ভূমিকা
- রেমডেসিভির একটি অপ্রমাণিত ট্রায়াল ড্রাগ